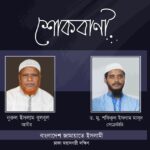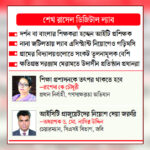অপরাধ সাংবাদিকতা: সমাজ রক্ষার এক অনিবার্য ঝুঁকি
বাংলাদেশে সাংবাদিকতা কখনোই নিরাপদ পেশা ছিল না। তবে গত পনেরো বছর- ২০০৯ থেকে ২০২৪ ছিল আরও অন্ধকার সময়। বাংলাদেশ কল্যাণ ট্রাস্টের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সময়কালে দেশে অন্তত ৬১ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। প্রতি মাসে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ জন সংবাদকর্মী হামলা, মামলা, হুমকি বা হয়রানির শিকার হয়েছেন। সব মিলিয়ে তিন হাজার পাঁচশতাধিক সাংবাদিক নানা ধরনের নির্যাতনের মুখে পড়েছেন। একই সময়ে বিশ্ব গণমাধ্যম স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ ৪৪ ধাপ পিছিয়েছে। এ পরিসংখ্যান শুধু কিছু সংখ্যা নয়, বরং সাংবাদিকতার ঝুঁকিপূর্ণ বাস্তবতা এবং রাষ্ট্র-সমাজের এক গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি।
অপরাধ সাংবাদিকতা আসলে কী?
আমরা সাধারণত অপরাধ সাংবাদিকতা বলতে খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই বা ডাকাতির মতো খবরকে বুঝি। কিন্তু এর পরিধি অনেক বড়। দুর্নীতি, রাজনৈতিক অপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক অপরাধ কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার—এসবই অপরাধ সাংবাদিকতার আওতায় পড়ে। মূল প্রশ্ন হলো, কোন প্রতিবেদন সাংবাদিককে ব্যক্তিগত ঝুঁকির মুখে ফেলে? সেটিই অপরাধ সাংবাদিকতা।
কার্ল বার্নস্টাইনে মতে, অপরাধ সাংবাদিকতার লক্ষ্য সত্যকে জনগণের সামনে আনা। কিন্তু এই সত্য প্রকাশ করা সহজ নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠী কিংবা অপরাধচক্র—সবাই চায় অপরাধ আড়াল করতে। সাংবাদিক যখন সেই পর্দা উন্মোচন করেন, তখন তার জীবন, নিরাপত্তা ও পেশাগত স্থিতি ঝুঁকির মুখে পড়ে।
কেন অপরাধ সাংবাদিকতা অপরিহার্য?
অপরাধ সাংবাদিকতা শুধু তথ্য প্রচার নয়; এটি সমাজ রক্ষার এক অপরিহার্য উপাদান।
• দুর্নীতি উন্মোচন: একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক যখন সরকারি প্রকল্পে লুটপাট প্রকাশ করেন, তখন তা রাষ্ট্রীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।
• মানবাধিকার রক্ষা: নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিক মহলেও চাপ তৈরি হয়।
• আইনের শাসন: অপরাধীদের প্রকাশ্যে আনা হলে ন্যায়বিচারের দাবিও জোরদার হয়।
অতএব, অপরাধ সাংবাদিকতা ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। জনগণ অন্ধকারে থাকে, অপরাধীরা নির্ভয়ে বেঁচে যায়।
বাস্তবতা: বাংলাদেশে ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণ:
বাংলাদেশে অপরাধ সাংবাদিকতাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র। শুধু সাধারণ অপরাধ নয়—দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে কাজ করলে সাংবাদিকরা সরাসরি টার্গেট হন।
সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা ভুলে যাইনি। ২০১২ সালে এই দুই সাংবাদিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আজও সেই ঘটনার বিচার হয়নি। বরং তদন্ত দীর্ঘসূত্রিতার আড়ালে চাপা পড়ে আছে। এই একটি উদাহরণই সাংবাদিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার চিত্র স্পষ্ট করে।
প্রতিবছরই বিভিন্ন অঞ্চলে সংবাদকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ক্ষমতাধর রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট প্রকাশ করলে সাংবাদিকদের জীবনের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে। অনেকে হামলার শিকার হয়েছেন, অনেককে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পেশাগত জীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছে।
ফলে অনেকেই ভয়ে নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকতা করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কেউ কেউ সরকারি প্রলোভন বা অর্থনৈতিক সুবিধায় তথাকথিত “ধন্যবাদ সাংবাদিকতা” করেছেন—যা শুধু সাংবাদিকতার মর্যাদাকেই খাটো করেনি, জনগণের আস্থাকেও নষ্ট করেছে।
আর্থিক নিরাপত্তা: ঝুঁকি ভাতার দাবি:
সাংবাদিকরা যে ঝুঁকির মধ্যে কাজ করেন, তার জন্য আলাদা প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।
• নিয়মিত বেতনের পাশাপাশি ঝুঁকি ভাতা চালু করা জরুরি।
• জীবনবীমা ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
• হামলা বা মামলার শিকার হলে আইনি সহায়তা তহবিল থাকতে হবে।
উন্নত বিশ্বে ইতোমধ্যেই এ ধরনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিকদের এই সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
নৈতিকতার প্রশ্ন:
অপরাধ সাংবাদিকতায় ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনি আছে নৈতিকতার চ্যালেঞ্জ। ভুয়া খবর, পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্ট কিংবা অর্ধসত্য প্রকাশ সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে। এ কারণে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি (১৯৯৩, সংশোধিত ২০০২) সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় হওয়া জরুরি।
সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ। দর্পণ যদি বিকৃত হয়, সমাজও বিকৃত প্রতিচ্ছবি দেখে। তাই নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা না করলে অপরাধ সাংবাদিকতার আসল লক্ষ্য পূরণ হবে না।
বিশ্ব প্রেক্ষাপট:
গ্লোবাল মিডিয়া স্বাধীনতার সূচকে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় সব দেশেই সাংবাদিকরা নানা ঝুঁকিতে আছেন। ভারতে বারবার গণমাধ্যমের ওপর হামলা হয়, পাকিস্তানে সাংবাদিক নিখোঁজ বা খুন হওয়ার খবর আসে নিয়মিত। তবে বাংলাদেশে পরিস্থিতি আরও জটিল, কারণ এখানে রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক চাপ ও আইনি হয়রানি একসাথে কাজ করে।
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেমন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (RSF) কিংবা কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (CPJ) বহুবার সতর্ক করেছে—বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে গণতন্ত্র আরও দুর্বল হয়ে পড়বে।
ভবিষ্যতের করণীয়:
১. গণমাধ্যম কমিশনের সুপারিশ: সাংবাদিকদের জন্য ঝুঁকি ভাতা, বীমা ও আইনি সহায়তা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
২. রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা: সাংবাদিক হত্যা বা হামলার বিচার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া নিরাপত্তা আসবে না।
৩. প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা সচেতনতা: সাংবাদিকদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি।
৪. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব: শুধু লাভ নয়, কর্মীদের নিরাপত্তা ও নৈতিক সাংবাদিকতা বজায় রাখাও তাদের কর্তব্য।
পরিশেষে বলা যায়, অপরাধ সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ—কিন্তু সমাজের জন্য অনিবার্য। দুর্নীতি, অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করতে সাহসী সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ানো রাষ্ট্র, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের দায়িত্ব।
কারণ অপরাধ সাংবাদিকতা না থাকলে সমাজ ধ্বংসের মুখে পড়বে, অপরাধীরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে, আর গণতন্ত্র হবে মুখোশবন্দী। তাই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানে কেবল একটি পেশাকে রক্ষা করা নয়; বরং দেশের গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা।
লেখক: সংবাদকর্মী
গাযী আনোয়ার
নির্বাহী সদস্য
ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)